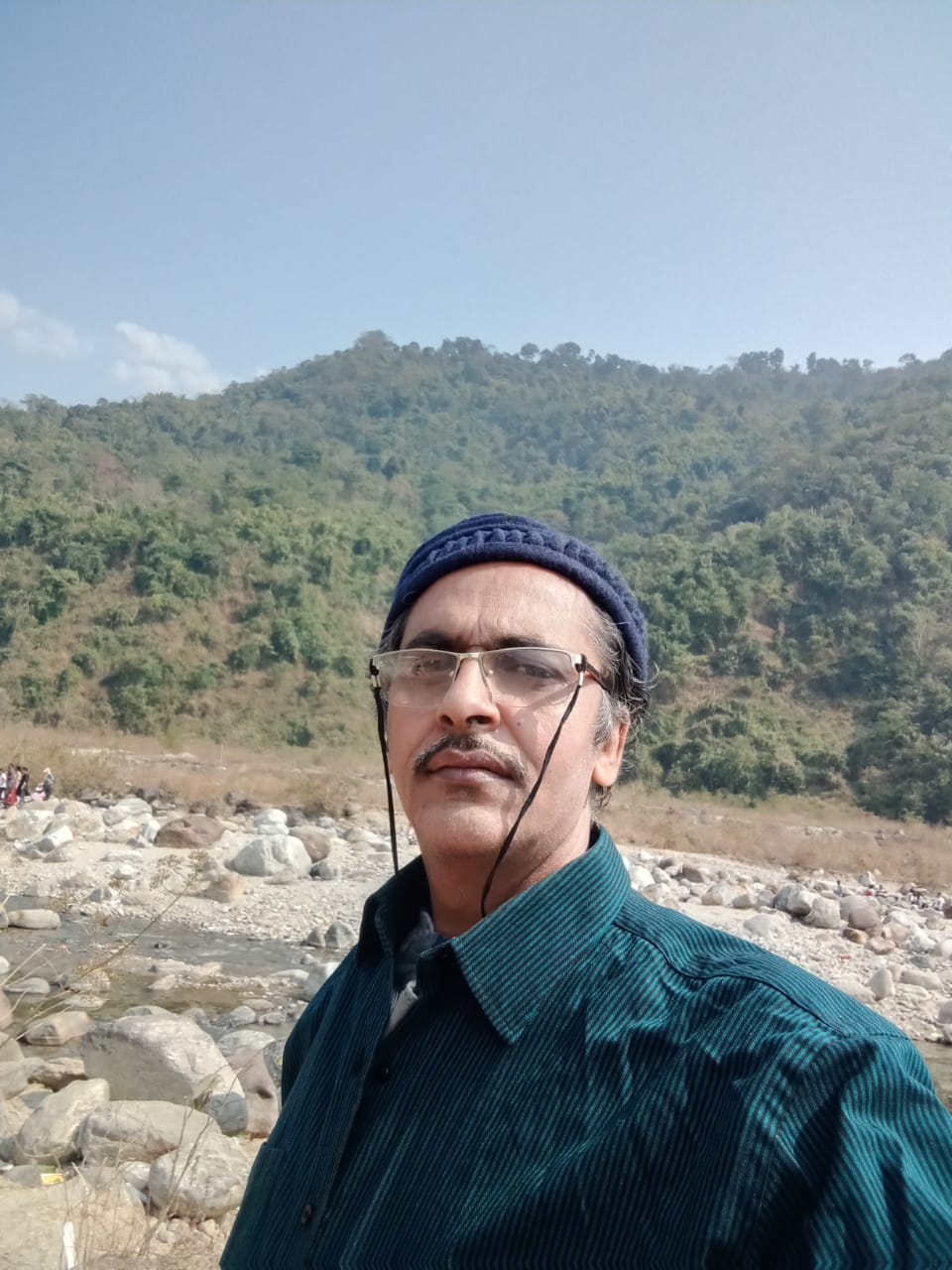সাহিত্যের ডাক্তার ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।আবার ‘শখের হোমিওপ্যাথ ডাক্তার বলে সমাদৃত ছিলেন।সাহিত্য তো সুহৃদয় হৃদয় সংবাদ।যে সাহিত্য মন-প্রাণকে শুদ্ধ ও পরিশিলিত করে সুস্থ যাপনের দিকে নিয়ে যায়।কবিগুরু ছিলেন সাধারণের জন্য নিবেদিত প্রাণ। চিকিৎসার প্রতি তার অনুরাগ ও অসুস্থের জন্য আসীম দরদ কবিগুরুকে সকলের আপনজনে পরিনিত করেছিল।সাহিত্যের ঐশ্বর্যের উচ্চ শিখরে অবস্থান করেও মানব সেবার তাড়নায় সাধারণের শুশ্রূষায় চিকিৎসক হিসাবেও সাধারনের মুশকিল আশান হতে হয়েছে কবিগুরুকে।কবির কথায়,যাদের সাধ্যগোচরে কোথাও কোন চিকিৎসার উপায় নেই,তারা যখন কেঁদে এসে পায়ে ধরে পড়ে তাদের তাড়া করে ফিরিয়ে দিতে পারি!এত বড় নিষ্ঠুর শক্তি আমার নেই।এদের সম্বন্ধে পণ করে বলতে পারিনে যে পুরো চিকিৎসক নই বলে চেষ্টা করব না’।
কবির সেবাব্রতী মনের পরিচয় পাই ১৯০১ সালে কলকাতার মানুষ যখন প্লেগ আতঙ্কগ্রস্ত।তিনি অসুস্থ শরীর নিয়ে সোজা কলকাতায় ফিরে যান।সেই সময় পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাহস যোগালেন মনিষী রবীন্দ্রনাথ।তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন।এ বিষয়ে ছিল তাঁর গভীর পড়াশোনা।জানা যায় কবিকে ডাক্তার বলে সম্বোধন করলেই বেশি খুশি হতেন।শান্তি নিকেতনে আবাসিকদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধ্যে সচেতন ছিলেন।হাসপাতালে সপ্তাহে একদিন যেতে হত আবাসিকদের।১৯১৯ সালে হারাসান নামে এক জাপানী মেয়ে জ্বরে ভুগছিল।তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে শেষমেশ সুস্থ করে ছিলেন।পথ্যের পরামর্শও দিয়েছিলেন,বার্লির রস বা ডালের সুপ, মুর্গীর সুপ,সোডা,জলযুক্ত দুগ্ধ প্রভৃতি[সুত্র পশ্চিমবঙ্গ,রবীন্দ্র সংখ্যা পুরানো সংস্করণ]।রামগড়ে কবি পাহাড়ের বাসিন্দাদের কাছে ডাক্তার বলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।একজন কাঠের মিস্ত্রির স্নায়ুবিক ব্যধি কবির ওষুধ খেয়ে সেরে যায়।পাহাড়ের বাসিন্দাদের চিকিৎসার জন্য সাত সকালে লাইন পড়ে যেত।কবিগুরু তাঁর কাঠেরবাক্স থেকে রোগীদের হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিতেন।জীবাণু গঠিত জটিল চর্মরোগে আক্রান্ত রোগীকে কবিগুরু স্রেফ হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়ে সুস্থ করার কাহিনিও রয়েছে।বিশিষ্ট চিকিৎসক পশুপতি ডাক্তারও চেয়েছিলিন রোগীকে হাই-ডোজের ইঞ্জেকশন দিতে।না হলে সারা শরীরে রোগ সংক্রামিত হতে পারে।কবি সেই কথা শুনে হেসে বলেছিলেন,‘এখন তো আমারই ওষুধ চলুক,দু’দিন দেখায় যাক না কী হয়’।সত্যিই কবির কথায় ফলে গিয়েছিল,কবির ওষুধ খেয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে ছেলেটি।রবীন্দ্রনাথ তখন ডাক্তারবাবুকে রসিকতা করে বলেছিলেন,‘তোমারা আমাকে ডাক্তার বলে মানবে না!আমি ফি নিই না।তাই ডাক্তার নই।যদি মোটা ফি নিতাম সবাই বলত একজন মস্ত বড় ডাক্তার’।১৯১৮ সাল ইনফ্লুয়েঞ্জা হানা দিয়েছিল বোলপুরের আশ্রমে।আশ্রমে অনেক ছাত্র-ছাত্রী শয্যাশায়ী।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোজ ঘুরে ঘুরে আক্রান্ত ছাত্রীদের দেখতেন।খোঁজ খবর নিতেন।তাদের জন্য নিম,গুলঞ্চ তেউরি,নিসিন্দা আর থানকুনি বেটে এই রামতেতো পাঁচন তৈরি হত।আশ্রমিকদের খাওয়াতেন।এই বিষয়ে খুব কড়া ছিলেন কবি।[সূত্র,প্রবন্ধ শ্যামল চক্রবর্তী]জানা যায় কবিগুরুর পাবনায় জমিদারী পরিচালনার সময় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও করতেন।নৌকাবাসের সময় নদীর তীরে বসবাসকারীদেরও চিকিৎসায় আগ্রহ দেখাতেন।শিলাইদহে থাকাকালীন ডাক্তার জগৎ রায়ের ঘনিষ্ঠ হন কবি।পদ্মাপাড়ের প্রজারা চিকিৎসা করাতে আসতেন।শিলাইদহে ডিসপেনসারিও খুলেছিলেন কবি।মংপুর রবীন্দ্র ভবনে কবির বায়োকেমিক ওষুধের সিসি সযত্নে রয়েছে।‘মংপুতে রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে মৈত্রী দেবী এক আলাপচারিতায় কবিকে বলছেন,সুধাকান্ত বাবু বলছিল কবিরাজি ওষুধ খাওয়া ধরেছেন..।‘এটাতে আমি খুব উপকার পাব’।‘হতে পারে,তবে কিনা এর মধ্যে কি আছে না আছে জানা নেই,লেখাও থাকে না,ডাক্তার আপনাকে যেটা খেতে বলেছেন সেটা আনিয়েনি বরং’।‘ঠিক এই কথায় তোমাদের কাছে আমি প্রত্যাশা করি।দাসমনোবৃত্তি একেই বলে।যেহেতু ওটা সাহেবের হাতে বিলেতে তৈরি,ওটা খারাপ হতেই পারে না।আর এটা অভাগা দেশে তৈরি হয়েছে কিনা,খারাপ না হয়ে যায় না!…তোমরা কিছুই জানো না’।বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক ডঃ রতন বিশ্বাস একান্ত আলাপচারিতায় জানান কবিগুরু কালিম্পঙে নিয়মিত গৌরিপুর ভবনের একতলায় বসতেন।পাহাড়ের বাসিন্দারা আসতেন সেখানে কবি স্বাস্থের খবর নিতেন।প্রয়োজনে চিকিৎসার পরামর্শ দিতেন।সাধারণ মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্তিম ভালোবাসা।কালিম্পঙেও ডাক্তার হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন’
কবি মনে করতেন জরাজীর্ণ শরীর কর্তব্য পালন করে পারে না।এই ব্যধি যেমন দারিদ্র্যের বাহন তেমনই দারিদ্র্য ব্যধিকে পালন করে।গ্রাম বাংলার স্বাস্থ্য নিয়ে তাঁর চিন্তার অন্ত ছিল না।স্বাস্থ্য সমস্যা ও দারিদ্রতা কবিকে ভাবাত।বলশেভিক রাশিয়ার স্বাস্থ্য শিক্ষার আয়োজন বিষয়ে কবি লিখেছিলেন,‘যা দেখছি আশ্চর্য় ঠেকছে।অন্য কোন দেশের মতই নয়।একেবারে মূলে প্রভেদ।কখনও লিখছেন,আমরা শ্রীনিকেতনে যা করতে পেরেছি এরা সমস্ত দেশজুড়ে প্রকৃষ্ট ভাবে তাই করছে।।…প্রতিদিনি আমি ভারতবর্ষের সঙ্গে এখানকার তুলনা করে দেখি আর ভাবি কী হয়েছে আর কি হতে পারত’।রবীন্দ্র নাথ চেয়েছিলেন মাতৃভাষায় সহজ সরল প্রণালীতে ব্যধি ও প্রতিকার নিয়ে লেখালিখি ও বই প্রকাশ হোক।স্বাভাবিকভাবেই ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্যের ‘আহার ও আহার্য’ বইটি পড়ে খুব খুশি হয়ে ছিলেন।কবিগুরুর অনুপ্রেনায় ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য, ‘ভারতীয় ব্যধি ও তাহার প্রতিকার’ নামে একটি বই লেখেন।যার ভুমিকায় কবি লেখেন “ডাক্তারি বইয়ের ভূমিকা কবি থেকে কবিরাজকে মানায় ভালো।এ কাজে আমার যদি সত্যিকারের তাগিদ থাকে,তবে সে রোগীর তরফ থেকে।কিছুকাল থেকে গ্রামের কাজে নিযুক্ত আছি,দেখেছি এদেশের সকলের থেকে গুরতর অভাব আরগ্যের।বিবিধ উপায়ে গ্রামের ঘরে ঘরে এদেশের লোককে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত কী করে রোগ ঠেকানো যায়।”কবিগুরু ছিলেন সংস্কার মুক্ত বিজ্ঞান সচেতন। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে ছিল তাঁর সম্যাক ধারণা।দেশি বিদেশি চিকিৎসকদের সঙ্গে ছিল তার হার্দিক সম্পর্ক।মানব দরদী কবি সম্রাট রবীন্দ্র সহজেই সাধারণের আপনজন হতে পেরেছিলেন।